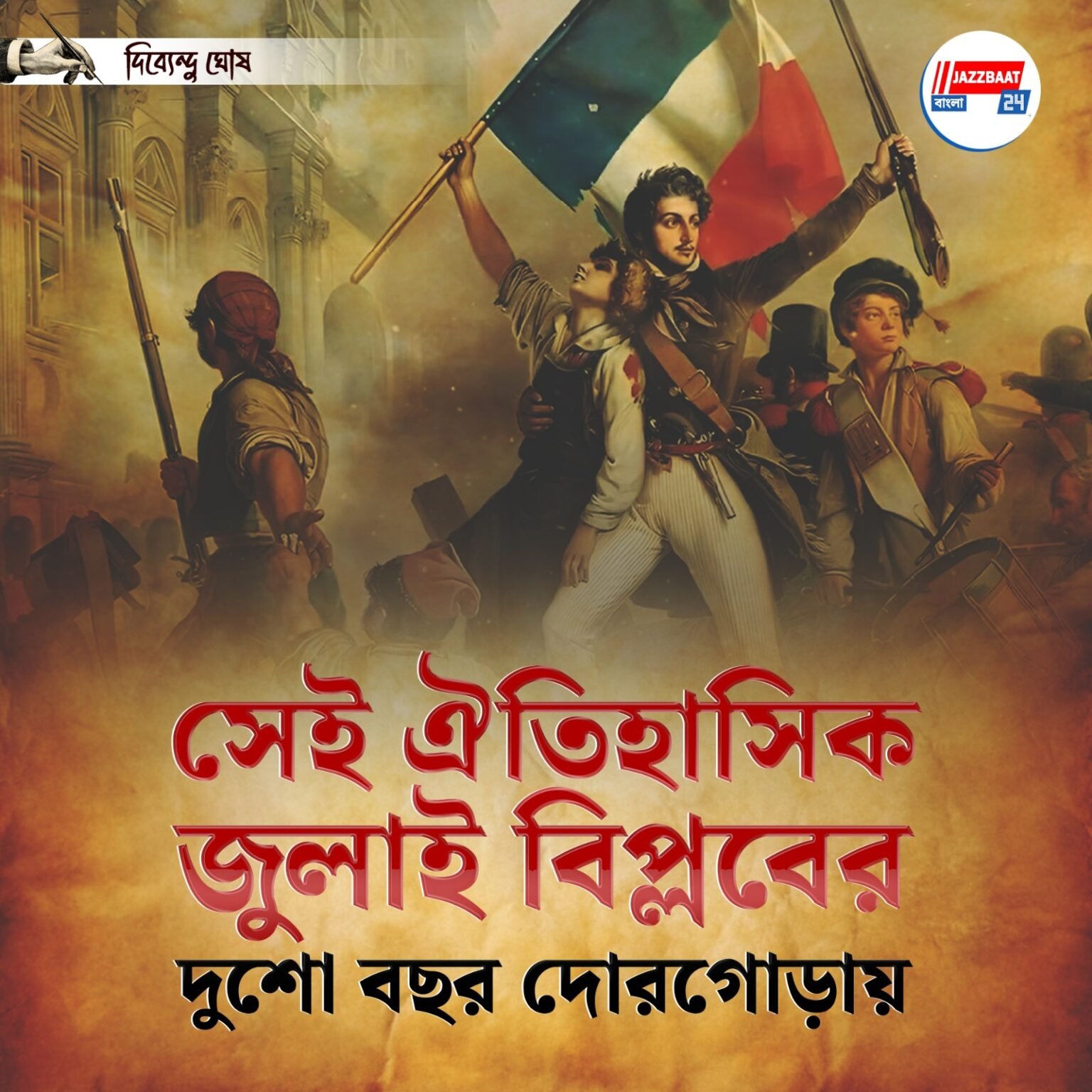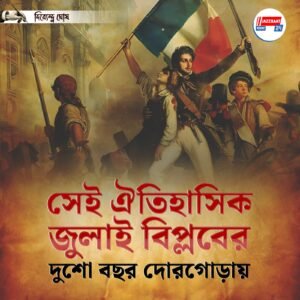দিব্যেন্দু ঘোষ
[ তিনদিনেই পালাবদল, দুশোর দোরগোড়ায় জুলাই বিপ্লব, ফ্রান্স ও ইউরোপের ইতিহাস ও বদলে দেওয়া অধ্যায় ]
১৮৩০ সালের জুলাই মাসের পর নতুন ভোর দেখে ফ্রান্স। ফরাসি আকাশ হয়ে ওঠে আরও স্বচ্ছ। মুছে যায় স্বৈরাচার। রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। লুপ্ত অধিকার ফিরে পায় ফ্রান্সের মানুষ। শুধু ফ্রান্সের ইতিহাস নয়, ইউরোপের ইতিহাসেও আমূল বদল আসে। জুলাই বিপ্লবের জেরে স্বাধীন হয় বেলজিয়াম। পোল্যান্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। প্রভাব পড়ে জার্মানি, স্পেন, গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে। জুলাই বিপ্লবের ছত্রে ছত্রে শোষণতন্ত্র মুছে যাওয়ার ইতিহাস। গণতন্ত্র ফিরে পাওয়ার তিনদিনের এক রুদ্ধশ্বাস বিপ্লব।
ফ্রান্সের যে বর্তমান প্রজাতন্ত্র, তা একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনির গোড়াপত্তন ১৮৩০-এর সেই ঐতিহাসিক জুলাইয়ে। ইতিহাসের হলুদ হয়ে যাওয়া পাতায় সেই লড়াইয়ের কথা সযত্নে ভাঁজ করে রাখা। সেই পাতা ওল্টানোর আগে বর্তমান শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া প্রয়োজন।এখনকার মতো আধা-রাষ্ট্রপতি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল না ফ্রান্সে। এখন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী দুজনেই দেশ চালানোর ক্ষমতা ভাগ করে নেন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান এবং তিনি সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। ফ্রান্সের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা পঞ্চম প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত, যার প্রতিষ্ঠা ১৯৫৮ সালে। ফ্রান্সের আইনসভার দুটি কক্ষ, জাতীয় পরিষদ ও সেনেট।
জাতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের ওপর নজর রাখে। সেনেটও আইন প্রণয়নে অংশ নেয়। তবে এর ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের চেয়ে কম। ফ্রান্সের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা একটি স্বাধীন বিভাগ, যা সংবিধান ও আইনের অধীনে কাজ করে।
ফ্রান্সের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে ফিরতে হলে প্রায় দুশো বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে। তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল দশম চার্লসের বিরুদ্ধে ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লব ঘটে। কিন্তু কেন ঘটল এই বিপ্লব?
সিংহাসনে বসেই সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি বাতিল করে দেন দশম চার্লস। তিনি ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও ক্যাথলিক গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন। বহু সাংবাদিককে জেলে ঢুকিয়ে দেন। দশম চার্লস ১৮২৭ সালে ধর্মবিরোধী আইন প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর গির্জার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। গির্জার বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকার কেড়ে নেন। জেসুইট নামক নির্বাসিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের দেশে ফিরিয়ে এনে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। ফ্রান্সের দেশত্যাগী অভিজাতদের জমির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৩০ সালের ২৫ জুলাই অর্ডিন্যান্স জারি করে নির্বাচিত আইনসভা ভেঙে দেন, বুর্জোয়া শ্রেণির ভোটাধিকার কেড়ে নেন, অষ্টাদশ লুইয়ের আমলের সনদ বাতিল করে দেন।
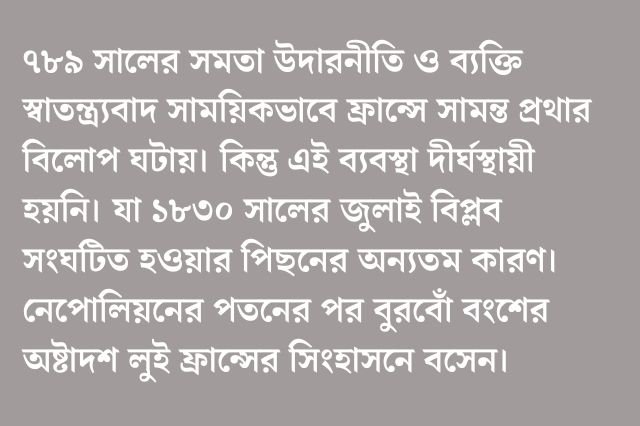
১৭৮৯ সালের সমতা উদারনীতি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ সাময়িকভাবে ফ্রান্সে সামন্ত প্রথার বিলোপ ঘটায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যা ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পিছনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়নের পতনের পর বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তিনি এই বংশের স্বভাবসুলভ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ঘটে, অষ্টাদশ লুই তাকে খুব একটা গুরুত্বই দেননি। কারণ তিনি ১৮১৪ সালে তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরকে তাঁর রাজত্বের ১৯ বছর বলে গণ্য করেন। কারণ ১৯ বছর আগে ষোড়শ লুইকে খুন করা হয়েছিল। তবুও অষ্টাদশ লুই আপসের নীতি নিয়ে রাজ্য শাসন শুরু করেন। বিপ্লবের ফলে ফরাসি সমাজে যে সব পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে পুরাতনতন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে উদ্যোগী হন অষ্টাদশ লুই।
ফ্রান্সের মানুষকে আশ্বস্ত করতে তিনি ১৮১৪ সালে একটি চার্টার বা সনদ দান করেন। এই সনদে রাজা শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব পান। যুদ্ধ, সন্ধি, বৈদেশিক নীতি, কর্মচারী ও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা পান রাজা। আইনসভা থাকলেও আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেন রাজাই। ৩০০ ফ্রাঁ কর প্রদানকারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে গোটা ফ্রান্সে মাত্র ৯০ হাজার লোক ভোটাধিকার লাভ করে। কোর্ড-নেপোলিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিপ্লবের সময়ের ভূমি সংস্কারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অধিকারে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় সব ক্ষমতা রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়। প্রজাতন্ত্র ভেঙে দেওয়া, মন্ত্রী নিয়োগ এবং সীমিত ভোটাধিকার জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অভিজাত আর ধনীরাই কেবল ভোটাধিকার পান। বঞ্চিত হয় সাধারণ প্রজা।
জাজবাত বাংলায় আরও পড়ুন
সনদের এই ভুলগুলো বুরবোঁ শাসনের সাফল্যকে ব্যাহত করে। শ্রেণি সংঘাত চরম আকার নেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটে। অষ্টাদশ লুইয়ের শাসনকালে কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এই দলগুলির মধ্যে বিরোধ ফ্রান্সকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। রয়্যালিস্ট দল দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণি ও ধর্মযাজকদের নিয়ে গঠিত হয়। এই দলের লক্ষ্য ফ্রান্সে যাজকতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সমিতি গঠন করে বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। অপর পক্ষ ১৮১৪ সালের সনদ অনুসারে আপসমূলক শাসনের পক্ষপাতী। উদারপন্থী অভিজাত বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল এদের সমর্থক। আবার উদারপন্থী দল মনে করত, ১৮১৪ সালের সনদ উদার নয়। তারা সনদ সংশোধন করে আইনসভাকে আরও শক্তিশালী করার পক্ষে। চরমপন্থী বা র্যাডিক্যাল নামে আরও একটি দল গড়ে ওঠে। এই দলের সদস্যরা ছিল নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণি। এরা মনে করত ১৮১৪ সালের সনদে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হবে না। গণভোট প্রবর্তন ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে ফ্রান্সে স্থিতি আসবে বলে তারা বিশ্বাস করত। এদের বলা হত সমাজতন্ত্রী। এদের সঙ্গে বোনাপার্টবাদীরা যোগ দেয়। একাধিক দল গড়ে ওঠা এবং তাদের মধ্যে বিরোধ ফ্রান্সকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়।
১৮১৪ সালের মে মাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের ফলে ফ্রান্স এবং ইউরোপের একটা বড় অংশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং প্রুশিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এই সিদ্ধান্তগুলি নেয়। রাজা অষ্টাদশ লুই যখন কোনও উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান, তখন দশম চার্লস সিংহাসন দখল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছেষট্টি বছর এবং তিনি আরও প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। তাঁর রাজত্বের আট মাসের মধ্যেই মানুষের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে। তাঁর সময়ে ধর্ম-বিদ্বেষ বিরোধী আইনে বলা হয়, যদি কেউ ইউক্যারিস্টের অপব্যবহার করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। দশম চার্লস ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রী দলের নেতা। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্যপন্থা নীতি পরিহার করে যাজক ও অভিজাততন্ত্র ফিরিয়ে আনা।
ধীরে ধীরে পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার কৌশল চার্লসের পছন্দ ছিল না। তাই তিনি মন্ত্রী ভিলিলকে পদচ্যুত করে উগ্র রাজপন্থী পলিন্যাককে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব দেন। পলিন্যাকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলির মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। এর মধ্যে ১৮৩০ সালের ভোটে আইনসভায় উদারপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তারা একটি প্রস্তাব এনে পলিন্যাক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার জন্য রাজার কাছে আবেদন জানান। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র ‘ট্রিবিউন’, ‘ন্যাশনাল’ প্রভৃতি গোঁড়া স্বৈরতন্ত্রী বুরবোঁ রাজবংশের জায়গায় অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাব দেয়। আইনসভায় উদারপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্যারিসের প্রজাতন্ত্রীদের বিরোধিতার মুখে পড়ে দশম চার্লস পলিন্যাকের পরামর্শে আইনসভা ভেঙে দেন।

রাজার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে দশম চার্লস ‘জুলাই অর্ডিন্যান্স’ জারি করে দেন। জুলাই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে উদারপন্থী ও প্রজাতন্ত্রী দলগুলো প্রতিবাদ জানায়। তারা প্যারিসের রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলে। রাজবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামে। প্যারিসের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়। জনগণের উগ্রমূর্তি দেখে দশম চার্লস জুলাই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নিলেও বিদ্রোহীরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। শেষ পর্যন্ত ৩০ জুলাই দশম চার্লস তাঁর নাতি ডিউক অফ বের্দোর কাছে পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বুরবোঁ বংশের দাবি উপেক্ষা করে অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে মনোনীত করে। আইনসভা লুই ফিলিপকে সাংবিধানিক রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। দশম চার্লস ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন।
জুলাই বিপ্লবের তিনটি দিন খুব উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের ইতিহাসে যা গৌরবময় দিন হিসেবে চিহ্নিত। ১৮৩০ সালের ২৫ জুলাই রবিবার, রাজা পলিন্যাকের চুক্তি অনুসারে, ডিক্রির মাধ্যমে ১৮১৪ সালের সনদ পরিবর্তন শুরু হয়। ‘জুলাই অধ্যাদেশ’ নামে পরিচিত তাঁর ডিক্রিগুলি ডেপুটি চেম্বার ভেঙে দেয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মুছে দেয়, ভবিষ্যতের নির্বাচন থেকে বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বাদ দেয় এবং নতুন নির্বাচনের ডাক দেয়। ২৬ জুলাই সোমবার, প্যারিসের নামী সংবাদপত্র ‘লে মনিটুর’-এ এই ডিক্রিগুলি প্রকাশিত হয়। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। বাইরে প্রচণ্ড গরম, শুষ্ক আবহাওয়া। যাদের সামর্থ্য ছিল তাদের প্যারিস ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই পারেননি। তাই তাঁরাই প্রথম জানতে পারেন, সেন্ট ক্লাউড অর্ডিন্যান্স তাদের চেম্বার অফ ডেপুটিজের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করে। যারা সামাজিক মর্যাদার চূড়ান্ত অধিকার চান তাদের জন্য এই ধরনের সদস্যপদ অপরিহার্য ছিল। প্রতিবাদে, বোর্সের সদস্যরা টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে এবং ব্যবসার মালিকরা তাদের কারখানা বন্ধ করে দেয়।
শ্রমিকদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য নির্বিচারে রাস্তায় নামানো হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে বেকারত্ব বেড়ে যায়। অতএব, বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। নতুন আইন মেনে ‘জার্নাল ডেস ডেবাটস’, ‘লে মনিটুর’ এবং ‘লে কনস্টিটিউনেলে’-র মতো সংবাদপত্রগুলি প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। সেই সময় শহরের এক ডজন সংবাদপত্রের প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক ‘লে ন্যাশনাল’-এর অফিসে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা একটি সম্মিলিত প্রতিবাদে সই করেন এবং তাঁদের সংবাদপত্রগুলি চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সন্ধ্যায়, যখন পুলিশ একটি সংবাদপত্র অফিসে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করে, তখন তাদের স্বাগত জানাতে জনতা উত্তাল হয়ে ওঠে, তাদের চিৎকার বলছিল, ‘À বাস লেস বোর্বনস!’ অর্থাৎ ‘বুরবোঁ নিপাত যাক!’ এবং ‘ভিভ লা চার্টে!’ অর্থাৎ ‘সনদ দীর্ঘজীবী হোক!’।
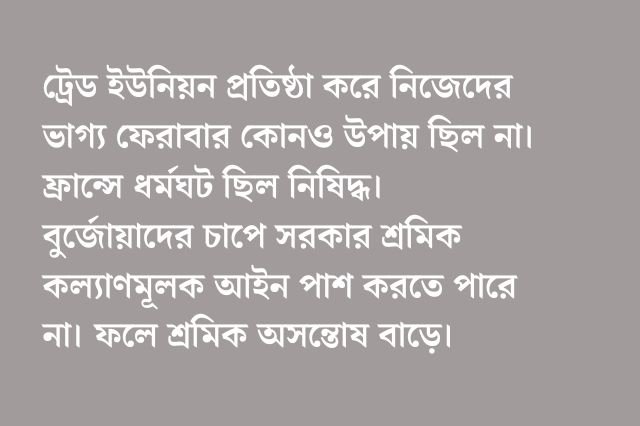
বিখ্যাত সাংবাদিক আরমান্ড ক্যারেল পরদিন ‘লে ন্যাশনাল’-এ লেখেন, ‘ফ্রান্স সরকারের পদক্ষেপের কারণেই বিপ্লব ফিরে আসে। আইনি শাসনব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। বলপ্রয়োগ শুরু হয়েছে। আমরা এখন যে পরিস্থিতিতে আছি, সেখানে আনুগত্য আর কর্তব্য নয়। দেখে নিতে হবে ফ্রান্স সরকারের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা। তা কতদূর প্রসারিত হতে পারে’। পুলিসের অভিযানের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ সত্ত্বেও, প্যারিসের পুলিস প্রধান জিন হেনরি ক্লদ ম্যাগিন সেই সন্ধ্যায় বিবৃতি দিলেন, ‘রাজধানীর সমস্ত অংশে নিখুঁত শান্তি বিরাজ করছে। আমার কাছে আসা প্রতিবেদনগুলিতে মনোযোগ দেওয়ার মতো কোনও ঘটনা লিপিবদ্ধ নেই’। মঙ্গলবার, ২৭ জুলাই ১৮৩০। জুলাই বিপ্লবের একটি সূচনাকারী ঘটনা, ‘লে ন্যাশনাল’-এর প্রেস বন্ধ করে দেওয়া হল।
সারাদিন ধরে জনতা রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন সংঘটিত করতে থাকে। সংখ্যাটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। প্যারিস অশান্ত হয়ে ওঠে। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ প্যারিসের প্রথম সামরিক বিভাগের সেনা কমান্ডার এবং গার্ড রয়্যালকে তাদের সৈন্য এবং বন্দুকগুলি টুইলেরিস, প্লেস ভেন্ডোম এবং প্লেস দে লা বাস্তিলের দিকে মুখ করে প্লেস ডু ক্যারোসেলে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, লুটেরাদের হাত থেকে বন্দুকের দোকানগুলি রক্ষা করার জন্য, শহর জুড়ে সামরিক টহল বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে, অস্ত্রভাণ্ডার বা বারুদ কারখানাগুলিকে রক্ষা করার জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সন্ধে ৭টায় গোধূলি আসার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।
প্যারিসের মানুষ সৈন্যবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। জানলা থেকে পাথর, ছাদের টাইলস এবং ফুলের টব রাস্তায় সৈন্যদের ওপর বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে থাকে। প্রথমে সেনা শূন্যে গুলি চালায়। কিন্তু রাত শেষ হওয়ার আগেই একুশ জন সাধারণ মানুষ মারা যায়। বিপ্লবীরা তখন নিহতের মৃতদেহ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে চিৎকার করতে থাকে, ‘মর্ট অক্স মিনিস্ট্রেস! À বাস লেস অভিজাত!’ অর্থাৎ মন্ত্রীদের মৃত্যু চাই, অভিজাতরা নিপাত যাক। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আমি দেখলাম উত্তেজিত জনতা পাশ দিয়ে চলে গেল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাদের পিছনে ছুটল। বিভিন্ন দিক থেকে আসতে থাকে অস্পষ্ট শব্দ, গুলির শব্দ, এবং তারপর কিছুক্ষণের জন্য আবার সবকিছু শান্ত।
আরও পড়ুন
কিছু সময়ের জন্য যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে শহরের সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সমস্ত দোকান বন্ধ; পন্ট নিউফ প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার, প্রতিটি রাস্তায় দৃশ্যমান স্তব্ধতা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল যেন, আমরা গভীর সংকটের মুখোমুখি হচ্ছি’। ১৮২৮ সালে, প্যারিস শহরে প্রায় ২০০০টি রাস্তার বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একাধিক ল্যাম্পপোস্টে ল্যাম্পগুলি লাগানো হয়েছিল। সংঘর্ষ প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত চলেছিল। ততক্ষণে রাস্তার সব বাতি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে রাতের অন্ধকার গাঢ় হতে থাকায় জনতা সরে যেতে বাধ্য হয়। বুধবার, ২৮ জুলাই ১৮৩০। হোটেল ডি ভিল দখল। প্যারিসে সারা রাত ধরে লড়াই চলতে থাকে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, ‘রাত সওয়া আটটা। চিৎকার আর গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ। রাস্তা দিয়ে ভিড় ছুটছে। কামান আর গুলির শব্দ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। À বাস লে রোই!, À লা গিলোটিন!, অর্থাৎ ‘রাজা নিপাত যাক, তাকে গিলোটিনে চড়ানো হোক’ ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে প্যারিসের পথঘাট’। চার্লস দশম গার্ড রয়্যালের কর্তব্যরত মেজর জেনারেল, রাগুসার ডিউক, মারেচাল অগাস্ট মারমন্টকে এই অশান্তি দমন করার নির্দেশ দেন। মারমন্ট ব্যক্তিগতভাবে উদারপন্থী ছিলেন এবং মন্ত্রিসভার নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাজার নির্দেশ পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এটা তাঁর কর্তব্য। রাজা সেন্ট ক্লাউডে থেকে যান। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা প্যারিসের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যাঁরা জোর দিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলেই সমস্যা মিটে যাবে। মারমন্টের পরিকল্পনা ছিল গার্ডে রয়্যাল এবং শহরের গ্যারিসনের লাইন ইউনিটগুলি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং সেতুগুলি পাহারা দেবে। পাশাপাশি প্যালেস রয়্যাল, প্যালেস ডি জাস্টিস এবং হোটেল ডি ভিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি রক্ষা করবে। দারুণ পরিকল্পনা ছিল, তবে পর্যাপ্ত সৈন্য ছিল না। গার্ডে রয়্যাল বেশিরভাগই অনুগত ছিল। তবে সংযুক্ত লাইন ইউনিটগুলি সংশয়ে ভুগছিল। অনেকে সেনার উর্দি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকে কেবল পিছিয়েই যাচ্ছিলেন। অন্যরা এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, কে তাদের দেখল তা ভেবে দেখছিল না।

প্যারিসে ব্যাঙ্কার ও কিংমেকার জ্যাক ল্যাফিট, ক্যাসিমির পেরিয়ার, জেনারেল এটিয়েন জেরার্ড এবং জর্জেস মাউটন, কমতে দে লোবাউ সহ আরও অনেক বুরবোঁ-বিরোধী মিলে একটি কমিটি তৈরি করেন। একটি আবেদনপত্র তৈরি করে সম্মিলিত স্বাক্ষরে তাঁরা অধ্যাদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। আবেদনপত্রটিতে রাজার নয়, বরং তার মন্ত্রীদের সমালোচনা বেশি ছিল। আবেদনপত্রে সই করে কমিটির সদস্যরা সরাসরি মারমন্টের কাছে যান রক্তপাত বন্ধের জন্য এবং সেন্ট ক্লাউড এবং প্যারিসের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন।
মারমন্ট আবেদনপত্রটি স্বীকার করেন। তবে বলেন, মীমাংসার জন্য প্যারিসের জনগণকে প্রথমে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। নিরুৎসাহিত কিন্তু হতাশ না হয়ে দলটি তখন রাজার মুখ্যমন্ত্রী ডি পলিন্যাকের সঙ্গে দেখা করে। সেখান থেকেও তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। পলিন্যাক তাঁদের সঙ্গে দেখাই করতে চাননি। তিনি জানতেন, এই আলোচনা মানে সময়ের অপচয়। মারমন্টের মতো তিনিও জানতেন যে দশম চার্লস ফ্রান্সের সিংহাসনের নিরাপত্তা এবং মর্যাদার জন্য অধ্যাদেশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। এইভাবে রাজা অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করবেন না। বিকেল ৪টে নাগাদ মারমন্টের অন্যতম প্রধান সহকারী কর্নেল কোমিয়েরোস্কি দশম চার্লসের কাছে একটি চিরকুট নিয়ে যান। তাতে লেখা, ‘মহাশয়, এটা আর দাঙ্গা নয়, এটা একটা বিপ্লব। মহাশয়ের জন্য শান্তির ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।
রাজমুকুটের সম্মান এখনও রক্ষা করা যেতে পারে। আগামিকাল হয়ত আর সময় থাকবে না। আমি অধৈর্য হয়ে মহাশয়ের আদেশের জন্য অপেক্ষা করছি’। রাজা পলিন্যাকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি প্রতিরোধের পরামর্শ দিলেন। বৃহস্পতিবার, ২৯ জুলাই ১৮৩০। কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার আলফ্রেড ডি ভিগনি লিখেছিলেন, ‘মানুষ তাদের জন্য মারা যাচ্ছে। একজন রাজপুত্রও আবির্ভূত হয়নি। রক্ষীবাহিনীর দরিদ্র লোকেরা আদেশ ছাড়াই, দুদিন খাবার ছাড়াই লড়াই করে যাচ্ছেন’। সম্ভবত একই কারণে, রাজপরিবারের সদস্যদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না; সম্ভবত আরেকটি কারণ ছিল যে এখন বিদ্রোহীরা সুসংগঠিত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল।
ইউটিউবেও জাজবাত, আপডেট থাকুন আমাদের সঙ্গে
মাত্র একদিন এবং একরাতে, শহর জুড়ে ৪,০০০-এরও বেশি ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল। বিপ্লবীদের ত্রিবর্ণ পতাকা, জনগণের পতাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলির ওপর উড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে সেন্ট ডেনিস, ভিনসেনেস, লুনেভিল অথবা সেন্ট ওমার থেকে অতিরিক্ত সৈন্য ডাকার জন্য মারমন্টের কোনও উদ্যোগ বা বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি রিজার্ভিস্ট বা দশম চার্লসের প্রতি অনুগত প্যারিসবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য চাননি। জুলাই বিপ্লবের বুরবোঁ-বিরোধী এবং সমর্থকরা পলিন্যাক এবং অন্য মন্ত্রীদের গ্রেফতারের দাবিতে তাঁর সদর দফতরে ভিড় জমান। অন্যদিকে বুরবোঁ সমর্থকরা এবং শহরের নেতারা দাঙ্গাবাজ এবং তাদের পুতুল প্রভুদের গ্রেফতারের দাবি জানান।
মারমন্ট কোনও অনুরোধেই কাজ করতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে রাজার আদেশের অপেক্ষা করেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ টুইলেরিস প্রাসাদটি লুটপাট করা হয়। রাজার বিধবা পুত্রবধূ এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর মা ডাচেস ডি বেরির বল ড্রেস পরা একজন ব্যক্তি, চুলে পালক এবং ফুল নিয়ে, প্রাসাদের জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলেন, ‘জে রেকোইস! জে রেকোইস!’ অন্যরা প্রাসাদের ভাণ্ডার থেকে ওয়াইন পান করছিল। লুটপাট চলে লুভরেও। সুইস সৈন্যরা জনতার মুখোমুখি হয়। গুলি চালানোর জন্য মারমন্টের নির্দেশের অপেক্ষা করছিল।
তবে তাঁদের অফিসাররা তাদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কারণ তারা ১৭৯২ সালের ১০ আগস্ট টুইলেরিস আক্রমণের সময় সুইস গার্ডদের ওপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি চাইছিলেন না। দুপুরের মাঝামাঝি হোটেল ডি ভিল দখল করে বিদ্রোহীরা। তবে এদিন লুটপাটের পরিমাণ কম ছিল। কেবল লুভর মিউজিয়ামের চিত্রকর্ম এবং শিল্পকর্মগুলিই নয়, তুইলেরিস, প্যালেস ডি জাস্টিস, আর্চবিশপের প্রাসাদ এবং অন্যান্য জায়গাগুলিও রক্ষা করেন স্থানীয় মানুষ। কয়েক ঘণ্টা পরে রাজনীতিবিদরা বিধ্বস্ত কমপ্লেক্সে প্রবেশ করেন এবং একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি নেন। যদিও পরবর্তী কয়েকদিন শহর জুড়ে লড়াইয়ের অবকাশ থাকলেও বিপ্লবের সমস্ত উদ্দেশ্য ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।
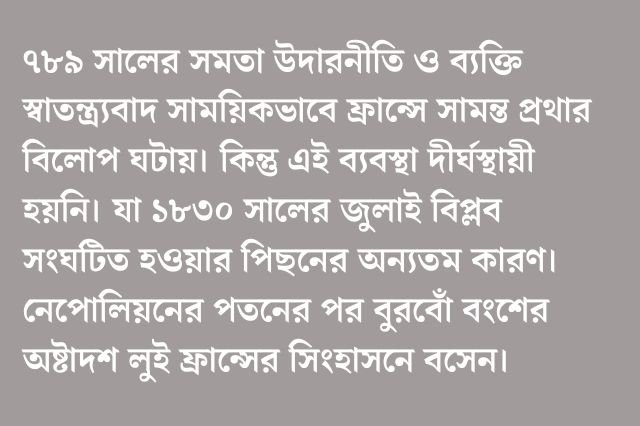
১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব আরেকটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের জন্ম দেয়। ২ আগস্ট, দশম চার্লস এবং তার পুত্র ডাউফিন সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে গ্রেট ব্রিটেনে চলে যান। যদিও চার্লসের ইচ্ছা ছিল তার নাতি, বোর্দোর ডিউক, হেনরি পঞ্চম হিসাবে সিংহাসনে বসুক। অস্থায়ী সরকার গঠনকারী রাজনীতিবিদরা তার পরিবর্তে অরলিয়ান হাউসের একজন দূরসম্পর্কের কাকার ছেলে লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসান। তিনি জুলাই রাজতন্ত্র নামে পরিচিত একটি সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দেশ শাসন করতে সম্মত হন।
এই নবায়িত ফরাসি বিপ্লবের ফলে ব্রাসেলস এবং নেদারল্যান্ডসের যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে আগস্টে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, যার ফলে পৃথকীকরণ এবং বেলজিয়াম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রান্সউইকে একটি সফল বিপ্লবও হয়েছিল। জুলাই বিপ্লবের উদাহরণ ইতালিতে ব্যর্থ বিপ্লব এবং পোল্যান্ডে নভেম্বরের বিদ্রোহকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৮৩২ সালে, প্যারিসের রিপাবলিকানরা, বিদ্রোহের ফলাফল এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দেখে হতাশ হয়ে, জুন বিদ্রোহ নামে পরিচিত একটি ঘটনায় বিদ্রোহ করে। যদিও এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল।
নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনের মাধ্যমে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ফরাসি বিপ্লব-উত্তর কালে ফ্রান্সে যে গণতান্ত্রিক বা উদারনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা একেবারে মুছে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে অষ্টাদশ লুইকে পুরাতনতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবী ব্যবস্থার সামঞ্জস্য করতে হয়। ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময় সামন্ত শ্রেণির অবসান ঘটে। জমিদারি কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। গির্জার সম্পত্তি কৃষকদের হাতে এসে পড়ে। এই সকল জমি পুনরায় সামন্ত শ্রেণি ও গির্জা মালিকানায় ফেরত দেওয়া সম্ভব ছিল না।
গ্রাম্য জীবনে এদের প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল বেশি, তাই গির্জা আর সামন্ত প্রভুর ক্ষমতা ছিল না তাদের উচ্ছেদ করার। ফ্রান্সের নবকৃষক শ্রেণির আশঙ্কা ছিল যে বুরবোঁ রাজ এবং অভিজাতরা ক্ষমতায় ফিরে এলে তাদের জমি হাতছাড়া হতে পারে। এ কারণে বুরবোঁ সরকারকে তারা সন্দেহের চোখে দেখত। অষ্টাদশ লুই জমির ওপর কৃষকদের অধিকার স্বীকার করে নিলেও কৃষকদের আশঙ্কা ছিল, ভোটাধিকার না থাকায় যে কোনও সময় আইনসভায় তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হতে পারে।
ফরাসি বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। প্রাক-ফরাসি যুগে যে অভিজাততন্ত্র ও কৌলিন্য প্রথা ছিল তার বিলোপ ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কলকারখানা ও ব্যবসা বিপুল বৃদ্ধি পায়। বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের তারতম্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। ধনী বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে ছিল ব্যাঙ্ক মালিক, শিল্পপতি, জাহাজ কোম্পানির মালিক। এরা ছিল খুব দাম্ভিক। এরা সহজেই অভিজাতদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল মূলত দোকানদার, চাকুরে, শিক্ষক, আইনজীবী প্রমুখ। এদের সংখ্যাই ছিল বেশি। শহরে শ্রমিক ও গ্রামের কৃষক শ্রেণির অবস্থান ছিল বুর্জোয়া শ্রেণির নীচে। শ্রমিকদের অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না।
জাজবাত বাংলায় আরও পড়ুন
ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ভাগ্য ফেরাবার কোনও উপায় ছিল না। ফ্রান্সে ধর্মঘট ছিল নিষিদ্ধ। বুর্জোয়াদের চাপে সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন পাশ করতে পারে না। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ে। শিল্প শহরগুলিতে শ্রমিক ও জনতা বিপ্লবমুখী হতে থাকে। গ্রামের দরিদ্র কৃষকের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। তারা চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হত। দরিদ্র চাষিকে রক্ষা করার কোনও আইন না থাকায় তাদের ওপর শোষণ জারি থাকে। ফরাসি বিপ্লবোত্তর কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে।
লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ার ফলে শহরগুলিতে বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জল প্রভৃতির সঙ্কট দেখা দেয়। শিল্প শহরগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে বস্তির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ফ্রান্সে শিল্পের বিস্তার দ্রুত ঘটছিল। বস্ত্র, ধাতু ও কয়লা শিল্পের অগ্রগতি ঘটে। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি হয়। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশ থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানি কমিয়ে ফেলা হয়। শিল্পের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। ফ্রান্সে রেলপথ নির্মাণের কাজও পিছিয়ে থাকেনি। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার মাইল রেলপথ তৈরি হয়। ফ্রান্সে নতুন বন্দরও স্থাপিত হয়। এভাবে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।
ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ঠিক কেমন ছিল? স্বৈরাচার ধ্বংস। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগ বলেন, ‘দশম চার্লসের আমলে যে স্বৈরাচার স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল জুলাই বিপ্লব তা ধ্বংস করে’। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজবংশের পতন ঘটে এবং অর্লিয়েন্স রাজবংশের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত নন, তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র এবং জনগণই হল প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ফরাসি জাতির রাজা। বিপ্লবের পর রাজা লুই ফিলিপ একটি সনদ গ্রহণ করেন। তার রচয়িতা ছিলেন জনগণ, রাজা নন। তিনি ‘ফ্রান্সে
ব্যবহৃত ছবি সৌজন্যঃ পিক্সাবে