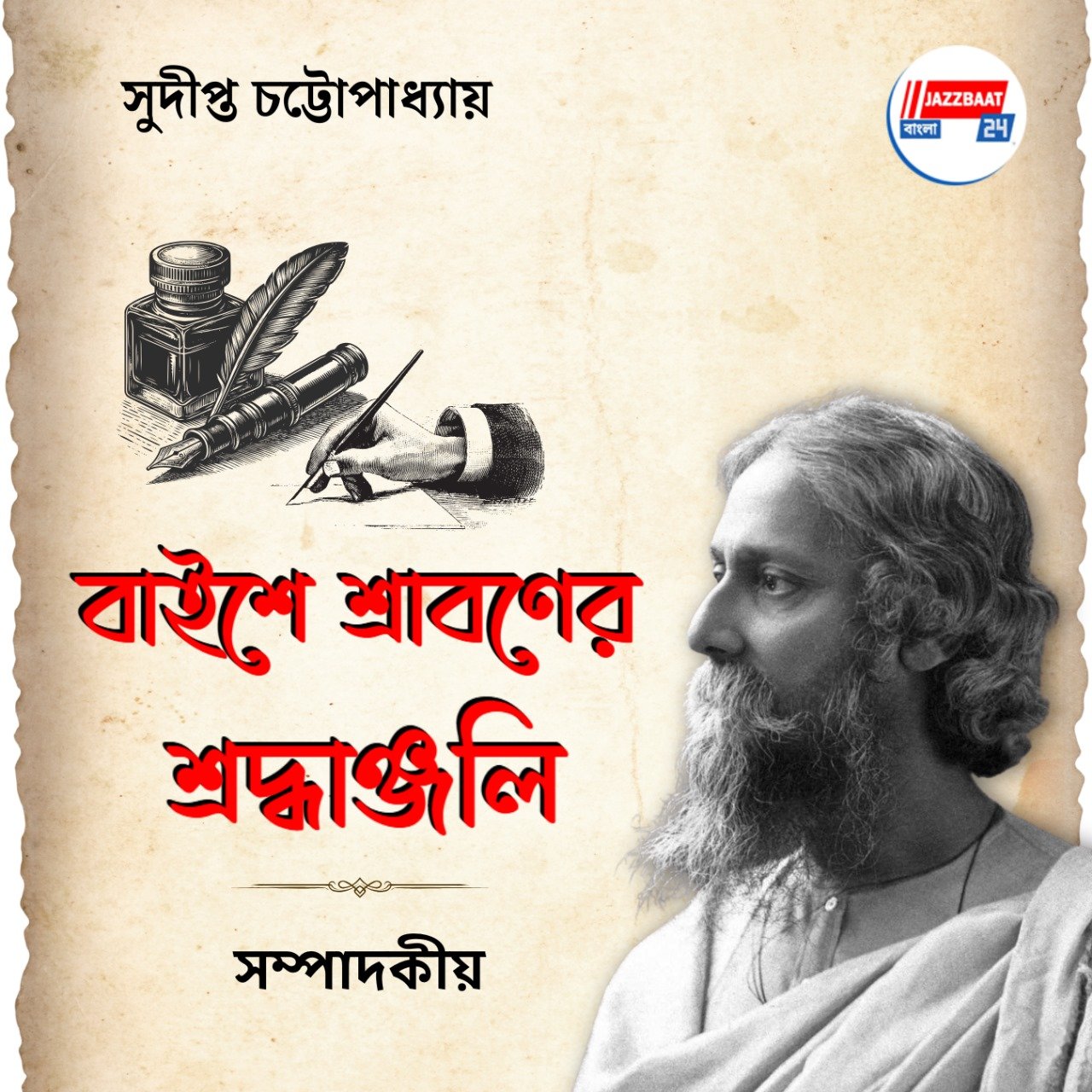জীবনভর দুঃখের বহমানতা শাণিত করেছিল রবীন্দ্র সৃষ্টিকে
“যখন মৃত্যু এসে আমাকে ফিসফিসিয়ে বলবে, তোমার দিন শেষ, আমি তাকে বলতে চাই, আমি প্রেমে বেঁচে আছি, কেবল সময়ের মধ্যে নয়। সে জিজ্ঞাসা করবে তোমার গান কি থাকবে? আমি বলব, আমি জানি না, কিন্তু এটা আমি জানি যে প্রায়শই যখন আমি গান গাইতাম তখন আমি আমার অনন্তকাল খুঁজে পেতাম।”
জীবন-মৃত্যুকে এভাবে যিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনিই আমাদের প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ। জীবনের পরতে পরতে যিনি মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথ।
” মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটা একটা দ্বীপের মত, চারিদিকে অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্ঠিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।
যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন ঐ অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাওয়ায় সময় হল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্ত নেবে, একটি কথাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে “সঙ্গে আমাকেও নাও — আমাকেও রাখো”, তখন সংসার বলে “তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের যা কিছু ফসল তা সমস্তই রাখব, তুমি তো রাখবার যোগ্য নও। “
প্রত্যেক মানুষ তার জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না– কিন্তু মানুষ যখন তার অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চায় তখন তার চেষ্টা বৃথা হয়। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকে তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসেব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনওমতে জমাবার জিনিস নহে।।
‐—-‐ সোনার তরী কবিতার মধ্য দিয়ে ঠিক এভাবেই জীবন-মৃত্যুর পথ চলাকে বর্ণনা করেছিলেন যিনি, তিনিই আমাদের কবিগুরু।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে যত দুঃখ বহন করেছেন তা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকের জীবনে ঘটেছে বলে জানা নেই। ১৩ বছর বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁর বিয়ের রাতে ভগ্নিপতি মারা যান। চারমাস পরে আত্মহত্যা করেন যার প্রেরণা ও ভালোবাসায় তিনি কবি হয়ে উঠেছেন, সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। ১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী ২৯ বছর বয়সে মারা যান। রবীন্দ্রনাথ তখন একচল্লিশ।
১৯০৫-এ প্রয়াত হন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের (১২ বছর) কলেরায় মৃত্যু। মেয়েদের বিয়ের সময় শর্ত অনুযায়ী জামাইদের ব্যারিস্টারি ও ডাক্তারি পড়াতে বিলেত পাঠালেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রেনুকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাঁচানো গেল না তাঁকে। ১৯১৮ সালে বড় মেয়ে বেলা অসুস্থ। বেলাকে প্রতিদিন গাড়িতে করে দেখতে যেতেন কবি। বাবার হাত ধরে মেয়ে বসে থাকত বিছানায়। আর তখন রবীন্দ্রনাথের জামাই শরৎ টেবিলের ওপর পা তুলে সিগারেট খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেন। একদিন বেলাকে দেখতে গিয়ে মাঝপথে শুনলেন সে মারা গেছে। মেয়েকে শেষ দেখা না দেখে ফিরে এলেন বাড়ি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন “বাড়িতে এসে তিনি কাউকে বুঝতে দিলেন না কি শোকে, কি অপমানে, কি অসহ্য বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি সন্তানকে হারিয়েছেন।”
শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম লিখতে পারে—
“আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥”
হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প!
ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে দিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে, যাঁকে বিলাতে কৃষিবিজ্ঞানী করার জন্য প্রতিমাসে সেইসময় পাঁচশো টাকা করে পাঠাতেন। আর নগেন্দ্র চিঠি লিখে আরও টাকা পাঠানোর তাগাদা দিতেন। প্রত্যুত্তরে কবি লিখলেন, ” আমার জমিদারি থেকে প্রতিমাসে পাঁচশো টাকাই পাই, তার পুরোটাই তোমাকে পাঠাই।” সেই নগেন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে দুই সন্তান সহ মীরাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কবির তিন জামাই যাঁদের প্রত্যেককে বিদেশে পড়িয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে কবিকে দুঃখ দিয়েছেন। সারাজীবনে কবি দুঃখ পেয়েছেন বারেবারে, অপমানিত-উপেক্ষিতও হয়েছেন অসংখ্যবার।
আর্জেন্তিনার কবিপ্রেমী লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা করে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কবির নোবেল প্রাপ্তি নিয়েও কিছু লোক তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। চিঠি লিখে কবির কাছে জানতে চাইছেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার টেকনিক, সেক্ষেত্রে ভাবী পুরস্কার প্রাপক কবিকে অর্ধেক টাকা দিতেও রাজি। শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করতে এসে কেউ কবিকে বলছেন, রবিবাবু আপনি কি এখনও কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি? মানে অতোগুলো টাকা পাওয়ার পর আবার কেউ লেখে নাকি! অথচ অনেকেই জানতেন না নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটা প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবিশ যখন কবিকে দেন তখন কবির প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, ” যাক, ওই টাকায় এবার বিশ্বভারতীর সেচ খাল কাটার সংস্থানটা হবে।” যারা কবি বা লেখক তাঁরা সকলেই সমাজের কাছে একটা স্বীকৃতি চায়, রবীন্দ্রনাথ বহুদিন সেটা বাঙালি সমাজের কাছে পাননি। তাই নোবেল প্রাপ্তির পর তাঁকে যখন সংবর্ধনা দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, ” আমি এই সম্মানের পাত্রকে ওষ্ঠ পর্যন্ত তুলব কিন্তু গলা পর্যন্ত যেতে দেব না।” কতটা অভিমান ও দুঃখ থাকলে এ কথা বলা যায়!
আসলে দুঃখ কাকে বলে এর প্রায় সবই কবিগুরু পেয়েছিলেন এক জীবনে। স্ত্রী’র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেল ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ।। পুত্রশোকে কবি লিখলেন-
“আজ জোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।” কবি’র মনে হলো এই জোৎস্নায় কবিকে বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমী’র! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লিখলেন-
“আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।’
বিদায়কালেও অতিমাত্রায় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, প্রস্রাবের প্রদাহে। বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেষ বিদায়টাও পাননি। দূর সম্পর্কের এক নাতনি ছিলেন কবির শেষ বিদায়ের ক্ষণে। প্রথম যৌবনে কবি যে গান লিখেছিলেন, সেটাই যেন কবির শেষ জীবনে নির্মম সত্য—“আমিই শুধু রইনু বাকি। যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥”
আসলে রবীন্দ্রনাথের লেখনী যেমন একটি বহমান ধারা, তেমনি কবির জীবনে দুঃখ-কষ্ট-শোক-সন্তাপ সবকিছুই যেন একটি বহমান জীবনবোধ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ” পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেল না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে সব পাওয়া পেল না।”
‘রুদ্ধ গৃহ’-তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন– ” জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে, মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।”
মৃত্যু-দুঃখ-অপমান বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে শাণিত করেছে সৃষ্টিপথে, নির্মোহ করেছে জগৎ সংসারে, নস্টালজিক করেছে ক্ষণে ক্ষণে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, ” আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।” আমরাও যেন সদা তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি,
“ মনেরে আজ কহ যে/ ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যরে লও সহজে”।